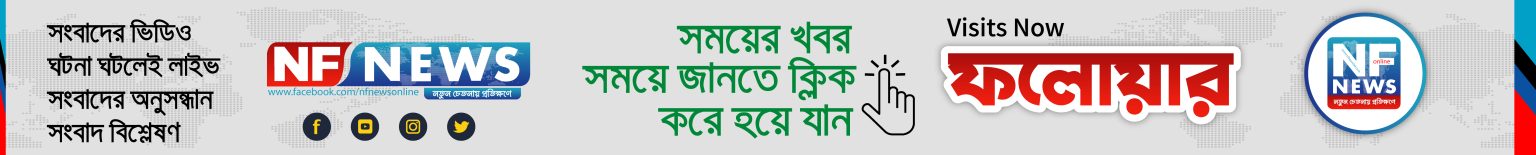তাঁতিদের মনোনিবেশ ও ছন্দময় ঠুকুর ঠাকুর শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে তাঁত বুনন—এটি নিছক কোনো কাজ বা পেশা নয়, বরং তাদের শৈল্পিক সৃষ্টির প্রকাশ। কখনও তারা বুনে ফেলেন জমকালো বেনারসি, কখনও সূক্ষ্ম কাপড়ের কুঁচি, আবার কখনও মোটা গামছা বা সাধারণ লুঙ্গি। তুলা থেকে সুতা উৎপাদন করে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হয়, যা ছোট হাতে বহনযোগ্য তাঁত থেকে শুরু করে বিশাল আকারের স্থির তাঁত পর্যন্ত হতে পারে।
আধুনিক বস্ত্র কারখানাগুলোতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত ব্যবহার হয়। ‘তাঁত বোনা’ শব্দটি এসেছে ‘তন্তু বয়ন’ থেকে, আর যারা এই কাজ করেন তাদেরই বলা হয় তাঁতি। ঐতিহ্যবাহী এই পেশার ধারক তাঁতিরা তাদের শৈল্পিক মননকে কাপড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যুগ যুগ ধরে।
গোড়ার কথা
বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং এটি দেশের বৃহত্তম কুটিরশিল্প। এই শিল্পের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁতশিল্পের সূচনা হয়েছিল আমাদের নিজস্ব তাঁতযন্ত্র এবং তুলা ব্যবহার করে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কাপড়ের চাহিদা পূরণে তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। চর্যাপদে তাঁতিদের জীবনধারা, তাদের কাজের গতি-প্রকৃতি, এবং তাদের শৈল্পিক উপস্থাপনার বিবরণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মিহি সুতার উল্লেখ আছে, যা তাঁতিদের কৃতিত্বকে তুলে ধরে। প্রাচীন বাংলার সুতিবস্ত্র উৎপাদনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। প্রথম খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মসলিন রোমে বিখ্যাত হয়ে ওঠে, যা বাংলার বস্ত্রশিল্পের সাফল্যের একটি উদাহরণ।

তাঁতি সম্প্রদায়ের বিবর্তন
শুরুতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কারিগররা তাঁতি পেশায় আধিপত্য বিস্তার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত আশ্বিনী তাঁতি নামে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের আসান তাঁতিরা নিজেদের প্রকৃত তাঁতি হিসেবে দাবি করেন এবং অন্যদের উপগোত্র বলে গণ্য করেন। তাঁতিরা তাঁদের পেশা উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন উপাধি, যেমন বসাক, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। ১৯২০-এর দিকে পূর্ববঙ্গে তাঁতিরা এসে বসতি স্থাপন করেন এবং বাংলার আসল তাঁতি বংশোদ্ভূত বলে গণ্য হন।
মুঘল ও ঔপনিবেশিক আমলের তাঁতিরা
মুঘল আমলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৫১৮ সালে পর্তুগিজ পরিব্রাজক দুয়ার্তে বারবোসা তার ভ্রমণ বিবরণীতে বাংলার বিভিন্ন কাপড়ের কথা উল্লেখ করেন। ঔপনিবেশিক শাসন দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং তাঁতিদের কাজ কঠিন করে তোলে। তবে, প্রায় এক শতাব্দী আগে, বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে বুনন মেশিন ছিল এবং স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেশজ কাপড়ের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরেও তাঁত শিল্পের প্রভাবশালী অবস্থান বজায় থাকে।
তাঁতিদের আধুনিক অবস্থা
বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলা হলো দেশের সবচেয়ে বড় তাঁতশিল্পের কেন্দ্র। এছাড়া, পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলার তাঁতিরাও সমৃদ্ধি লাভ করেন। বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে শাড়ি বুনন শুরু করেন এবং পরে তারা টাঙ্গাইলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেক বসাক তাঁতি ভারত চলে যান। টাঙ্গাইল ছাড়াও নরসিংদী, ডেমরা, শাহজাদপুর, কুমারখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁতিরা সমৃদ্ধি লাভ করেন।
আঞ্চলিক কাপড়ের গুণগত মানের ভিন্নতা দেখা যায়, যেমন রাজশাহীর সিল্ক, টাঙ্গাইল ও পাবনার সুতি শাড়ি, মিরপুরের কাতান ও জামদানি, ডেমরার বেনারসি, এবং নরসিংদীর লুঙ্গি। তাঁতিরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বাণিজ্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তাঁতিরা গ্রামের যে স্থানে বসবাস করেন তা তাঁতিপাড়া নামে পরিচিত। হস্তচালিত তাঁতগুলোতে চরকা বা সুতা কাটার টাকু ব্যবহার করা হতো, যা তাঁদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে ধারণ করে।
তাঁতিরা তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে যুগ যুগের ঐতিহ্যকে জীবিত রাখেন। যদিও তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত, তবুও রঙিন সুতায় বুনে যান স্বপ্নের জাল এবং নিজের ভবিষ্যৎ। তারা গান গেয়ে ওঠেন, “ভাদর মাসে কাটিলাম সুতা, আশ্বিন মাসের পয়লাতে…।”

বিশ্বরঙ–এর আয়োজনে তাঁত শাড়ির প্রদর্শনী
বিশ্ব রঙ সবসময়ই উৎসব পার্বন উৎযাপনে, দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ ২৩ আগস্ট ২০২৪ থেকে বিশ্বরঙ এর সকল শোরুমে এবং বিশ্বরঙ অনলাইনে শুরু হচ্ছে তাঁত শাড়ির প্রদর্শনী ‘তাঁতের মায়া’। এই প্রদর্শনীতে থাকছে ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির হরেক রকম ডিজাইনের আয়োজন। বিশ্ব রঙ শুভান্যুধায়ীদের জন্য প্রর্দশনীতে কেনা কাটায় থাকছে ৩০ শতাংশ মূল্য ছাড়।
তাঁতের শাড়ির প্রদর্শনীর সাথে থাকছে বিশ্ব রঙ এর নিয়মিত আয়োজন- শাড়ী, থ্রিপিছ, সিঙ্গেল কামিজ, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শার্ট, গহনা, ব্যাগ, গৃহসজ্জা সমগ্রী সহ আমাদের যাপিত জীবনের প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু। www.bishworang.com.bd এই ওয়েবসাইট এবং BISHWORANG ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অনলাইনে ঘরে বসেই কিনতে পারবেন আপনার পছন্দের পোশাকটি।